কলাম: নারী প্রশ্ন, শ্রেণি সংকট ও রাষ্ট্রের নীরবতা।
- সর্বশেষ আপডেট রবিবার, ২৫ মে, ২০২৫
- ৪৪ বার দেখা হয়েছে

রুদ্র নীল
বেশ কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি নরসিংদীর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক নাদিরা ইয়াসমিন নারীর উত্তরাধিকার, সামাজিক বৈষম্য এবং ক্ষমতার কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মৌলবাদী গোষ্ঠীর চক্ষুশূল হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে উঠেছে ‘ইসলামবিরোধী’ বক্তব্যের অভিযোগ। ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম, অপসারণের দাবি, ‘ঈমানহারা’ আখ্যা—এই প্রতিক্রিয়াগুলো কেবল একটি ব্যক্তির প্রতি ক্ষোভ নয়, বরং নারী স্বাধীনতা, শ্রেণিবৈষম্য ও রাষ্ট্রীয় নীরবতার এক জটিল সমীকরণ প্রকাশ করে।
এটি কি নিছক ধর্মীয় অনুভূতির আঘাত? নাকি ক্ষমতার একটি শ্রেণি-ভিত্তিক ব্যাখ্যা রক্ষা করতে গিয়েই এই প্রতিক্রিয়া? এ প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, কারণ নারীর উত্তরাধিকারের সমানাধিকার দাবি নতুন কিছু নয়, কিন্তু যখন তা একজন নারী শিক্ষকের মুখ দিয়ে, গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তখন প্রতিরোধটাও হয়ে ওঠে তীব্রতর।
বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইন এখনো ইসলামি শরিয়া অনুসরণ করে, যেখানে মেয়েরা বাবার সম্পত্তিতে ছেলের তুলনায় অর্ধেক পায়। এই আইন যে নারীর প্রতি সুস্পষ্ট বৈষম্যমূলক, তা বহুদিন ধরেই নারীবাদী চিন্তাবিদেরা বলে আসছেন। কিন্তু এই বৈষম্যের প্রশ্ন তুললেই যদি কাউকে নাস্তিক, ইসলামবিদ্বেষী বা সমাজবিধ্বংসী বলা হয়, তাহলে সেখানে কোনো যুক্তিবাদী সংলাপের জায়গা থাকে না। বরং তা হয়ে ওঠে একটি শ্রেণিশাসিত ন্যারেটিভ, যেখানে ক্ষমতার মালিকানা নির্ধারণ করে পিতৃতান্ত্রিক, ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারী গোষ্ঠী।
এই ক্ষমতার কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণকে একমাত্র ‘সত্য’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার মধ্যেই নিহিত থাকে সামাজিক শ্রেণি দ্বন্দ্বের আসল রূপ। কারণ, সম্পদ বণ্টনের প্রশ্নটি কেবল ধর্মীয় নয়, এটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। Judith Butler-এর ‘Gender Performance’ ধারণা অনুযায়ী, সমাজ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়, এবং সেই ভূমিকা পালনের বাইরে গেলেই নারীকে বিপজ্জনক মনে করা হয়। নাদিরা ইয়াসমিন সেই বিপজ্জনক ‘অভিনয়ভঙ্গ’ করেছেন বলেই আজ তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া।
এখানে আরেকটি বড় প্রশ্ন হলো—রাষ্ট্র কোথায়? যখন একজন সরকারি কর্মচারী, যার দায়িত্ব জনগণকে সচেতন করা, তিনি যদি নাগরিক অধিকারের পক্ষে কথা বলেন, এবং সেই কারণে যদি তাকে অপসারণের হুমকি দেওয়া হয়, তখন রাষ্ট্র কেন নীরব? এটা কেবল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করা নয়, বরং তা নারীকে ঘরের কোণে বন্দী করে রাখার পিতৃতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বৈধতা দিচ্ছে।
নাদিরা ইয়াসমিনের মতো কেউ যখন ‘হিস্যা’ নামের ম্যাগাজিনে উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন তিনি শুধু একটি আইন নয়, একটি দমনমূলক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানান। তাঁর বিরুদ্ধে যারা মাঠে নামে, তারা মূলত এই কাঠামোর সুবিধাভোগী। তাদের ভয়—যদি নারীরা কথা বলে, তাহলে আর পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা চলে না। এই ভয় থেকেই আসে ফতোয়া, আল্টিমেটাম, ঈমানহানির শিরোনাম।
আমরা আজ এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে অধিকারের কথা বললেই ধর্ম চলে যায়, মানবতার পক্ষে দাঁড়ালেই বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হতে হয়। অথচ সত্য হলো, ধর্মের প্রকৃত মর্মবাণী বিচার করলে নারীর মর্যাদা, সমান অধিকার ও ন্যায়ের কথাই উঠে আসে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যাকে চাপা দিয়ে ধর্মকে শাসনের যন্ত্র বানানোই যেন উদ্দেশ্য।
অতএব, এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন যুক্তি ও মানবিক মূল্যবোধের পক্ষেই দাঁড়ানো। প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নারীর স্বাধীন মতপ্রকাশ রক্ষা করা। কারণ, একটি সমাজ কেবল রুটির ন্যায্যতা দিয়ে টিকে থাকে না, প্রয়োজন সম্মান, প্রশ্ন করার অধিকার, এবং চিন্তার মুক্ত পরিবেশ।
নাদিরা ইয়াসমিন একা নন। তিনি সেইসব নিরব নারীর প্রতিধ্বনি, যাদের অধিকারের প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে বর্জিত। এবং সত্যকে দমন করা গেলেও নির্মূল করা যায় না—সে ফেরে অন্য নামে, অন্য মুখে।

কবি রেজাউল করিম রুমী এর কবিতার বই “”গোধূলি অগন্তুক “”আসছে ২০২৫ এর বইমেলায় আশাকরি পাঠক হৃদয় ছুয়ে যাবে।
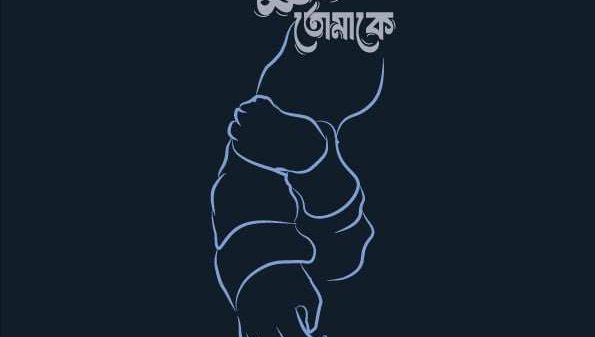
কবি নির্মলকুমার রায়ের নতুন কবিতার বই আসছে ২০২৫ এর বইমেলায়”” জল ছুঁই তোমাকে আশাকরি পাঠক হৃদয় ছুয়ে জাবে “”

পবিত্র ঈদুল আযহার মহান আদর্শ ও শিক্ষা কে আমাদের চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলন করতে হবে-দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

অভিনন্দন ইনডেক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রুপ সিইও জনাব শফিউল্লাহ আল মুনির গত ৭ জুন ২০২৪, রোজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের আউলিয়া নগরে খানকা শরিফ প্রাঙ্গণে ‘ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিকে’র শুভ উদ্বোধন করার জন্য

পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছোনগাছা ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন

মুন্সীগঞ্জে টঙ্গীবাড়ীতে পুরা দুর্গা চরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৪-২৬ ইং নবনির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হলেন সাবিত বিন শহীদ ।

ফরিদপুরে কম্পিউটার ট্রেন এর যাত্রা বিরতির আবেদন নিয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে – ড. যশোদা জীবন দেবনাথ (সিআইপি)

মুন্সীগঞ্জে টঙ্গীবাড়ী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাহবুবুর রহমান (মটর সাইকেল মার্কা) পেলেন।

মুন্সীগঞ্জে মেমোরা গ্লোবাল লিমিটেডের মু্ন্সীগঞ্জ জেলা শাখা আয়োজনে আলোচনা ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ।

প্রসাশনের চোখের সামনে আদালত অবমাননা করে চলছে মাটি খননের কাজ! থানার হস্তক্ষেপ চেয়েও মিলছে না প্রতিকার।

টঙ্গীবাড়িতে হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রা. আদর্শ মহিলা মাদরাসা, ইয়াতীম খানা, লিল্লাহ বোর্ডিং ও সমাজবাসীর উদ্যোগে মাদরাসা ময়দানে ৩য় বার্ষিকী ওয়াজ মাহফিল অনুষ্টিত ।

আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে পিরোজপুর জেলার ৩টি আসনে ৩জন আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবাই আলোচনার শীর্ষে

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার নবাগত ওসি বলেন মাদকের গ্রাস থেকে কিশোর- যুবকদের রক্ষা করতে হবে, সমাজ রক্ষা করতে হবে।

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে চৌবাড়ী সাবের মেহেরুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

পরীক্ষার পূর্বেই চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম প্রকাশতাড়াশ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের ৬০ লাখ বাণিজ্যের অভিযোগে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পঞ্চম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপ “বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ” শীর্ষক একটি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বাণী মহানবী (সা.) সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন : বাংলাদেশ ন্যাপ

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিঃস্বার্থভাবে বাংলাদেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করেন-দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও রাষ্ট্র্র ক্ষমতায় রাখতে নৌকা প্রতীকের জন্য ভোট প্রার্থনা-দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

ফরিদপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক শংকর সাহাকে অপমানের প্রতিবাদ জানাই -ড.যশোদা জীবন দেবনাথ

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী ও ১৫আগষ্ট এর ইতিহাস তুলে ধরতে-দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

সিরাজগঞ্জে পৌর কাউন্সিলর কর্তৃক কৃত্রিম জলাবদ্ধতা নিরসনে জেলা প্রশাসক বরাবর অভিযোগ দেবার পরও কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করায় জনমনে ক্ষোভ

সিরাজগঞ্জে দলের নাম ভাঙ্গিয়ে ভিজিএফ’র চাউলের বস্তা ব্যাপারীর মাথায় তুলে দিলেন – ইউপি চেয়ারম্যান নান্নু

সিরাজগঞ্জ ছোনগাছায় কাবিখা- কাবিটা প্রকল্প পরিদর্শন করেন – এমপি জয়প্রশংসায় ভাসছেন আবদুল্লাহ আল মামুন















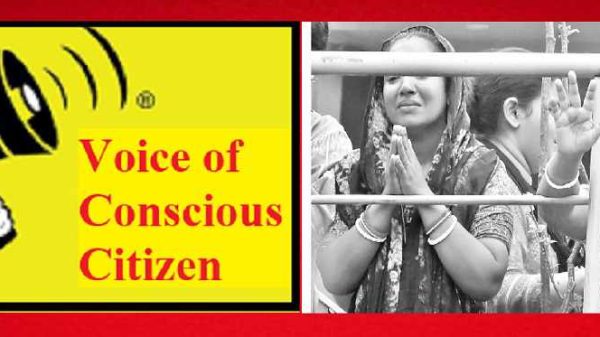

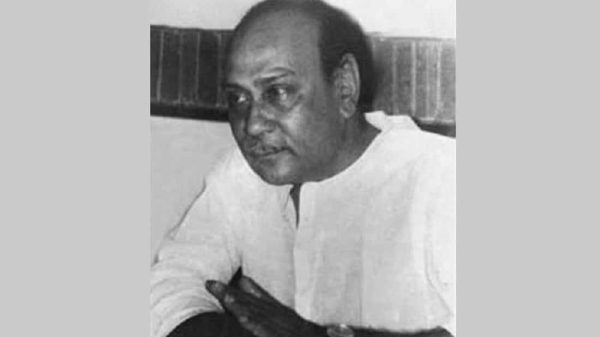


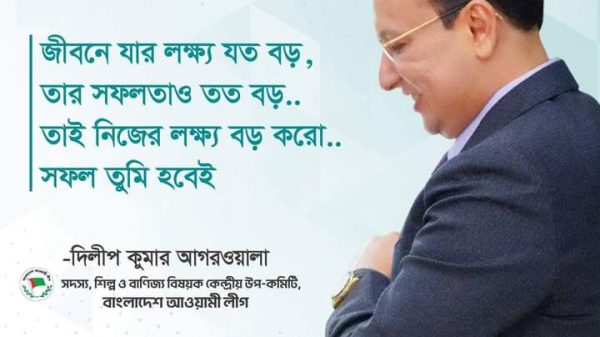


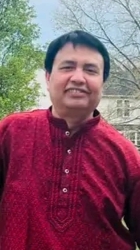








































































































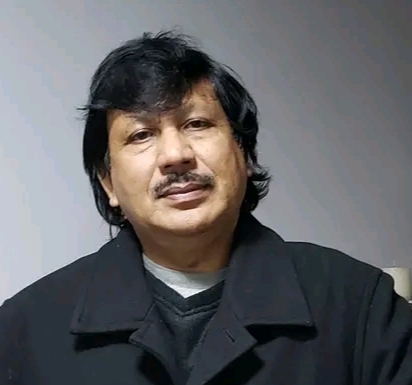



























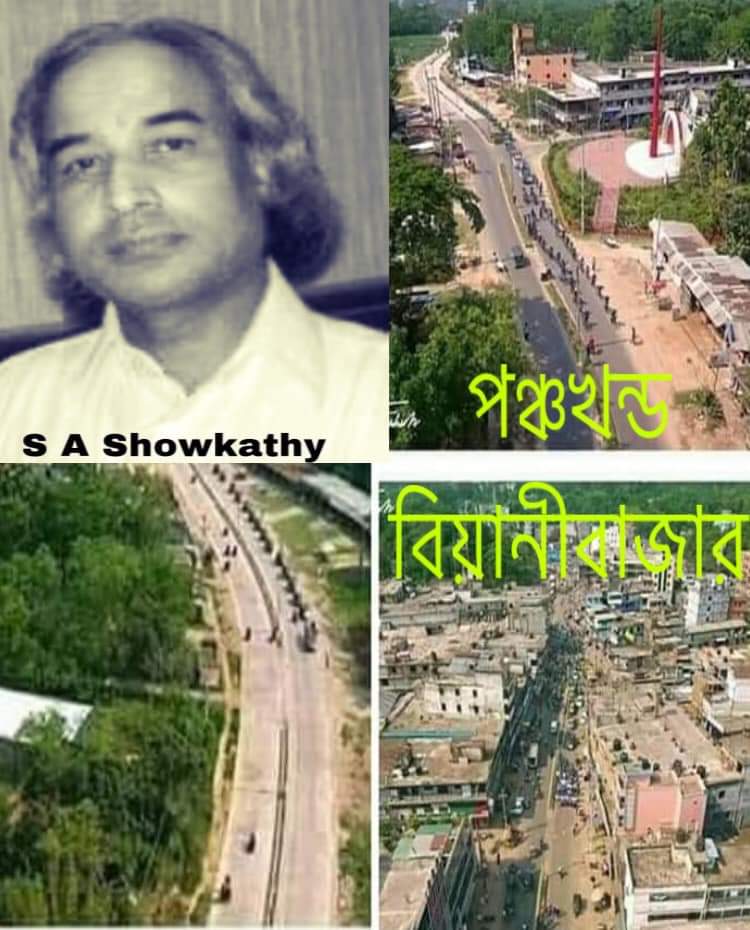
















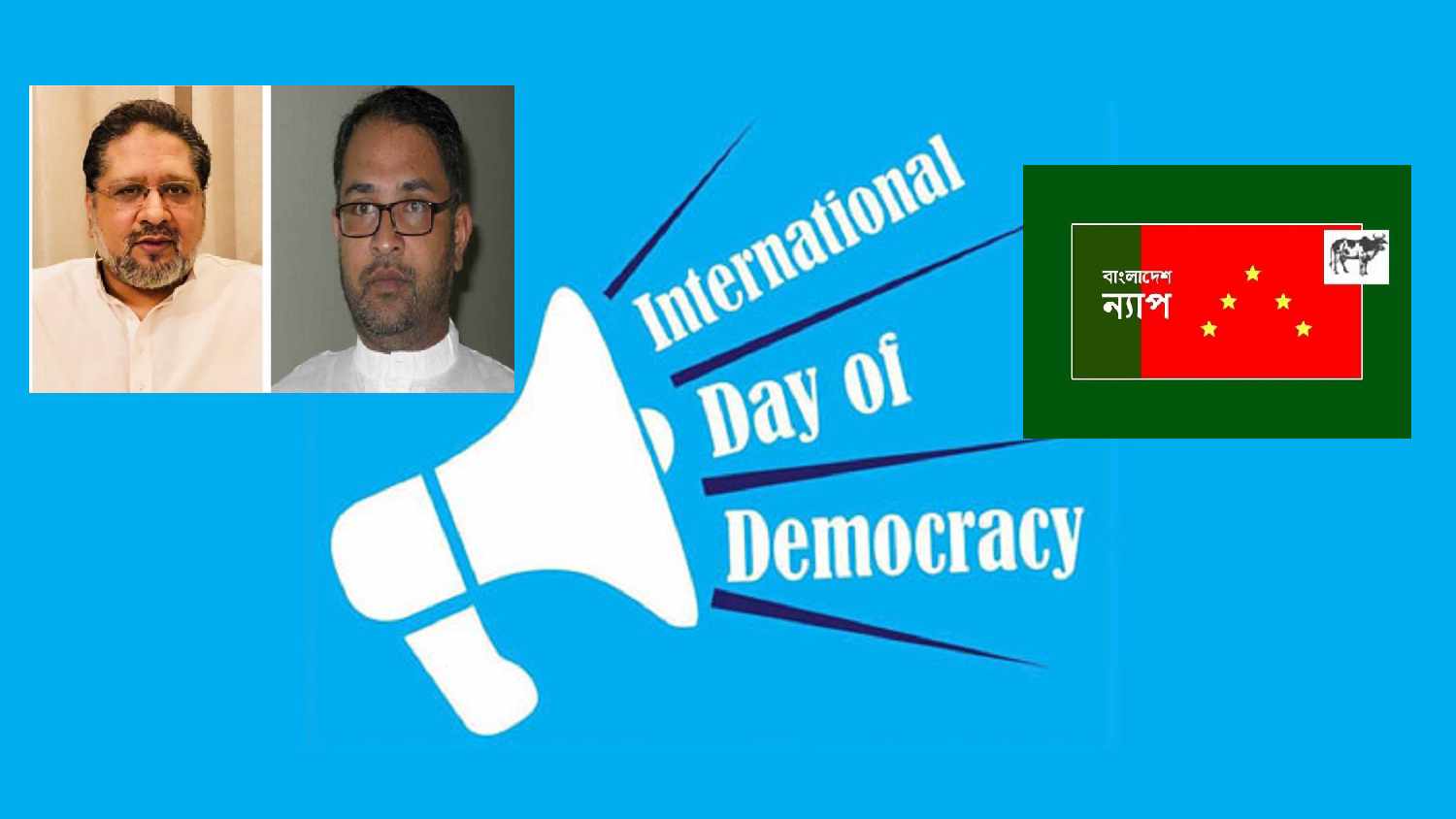

















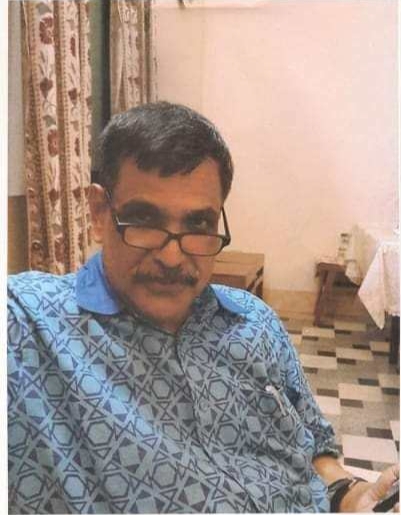





































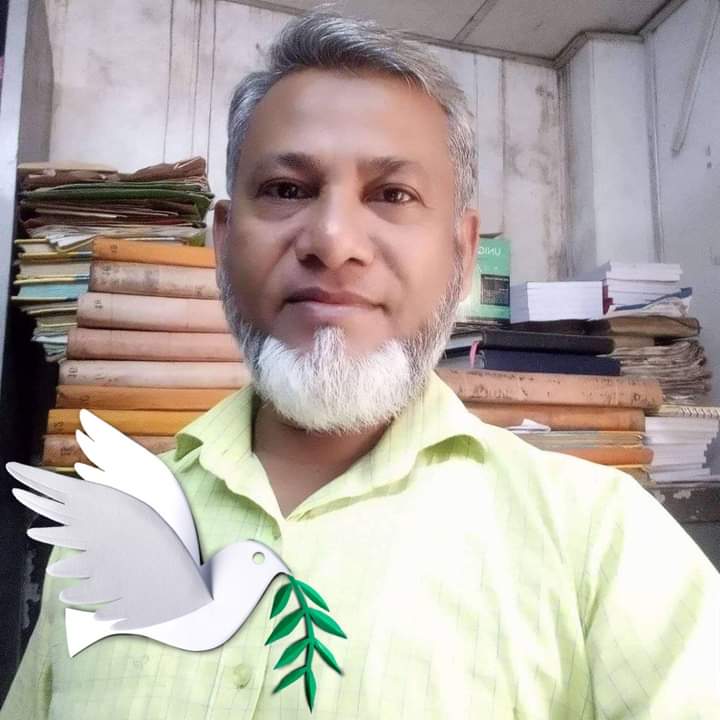




















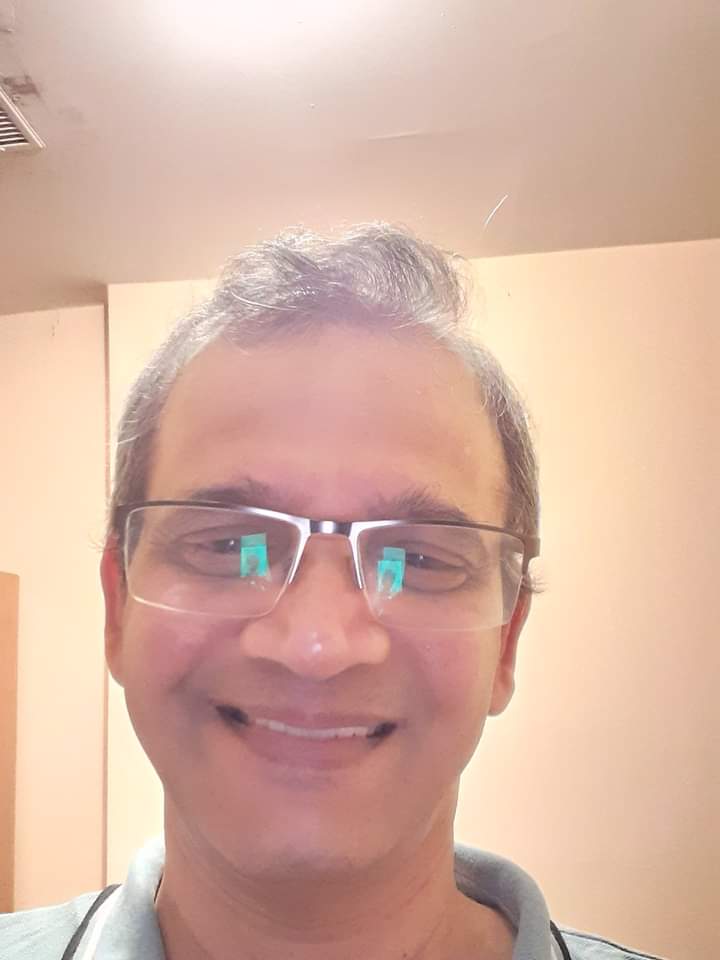








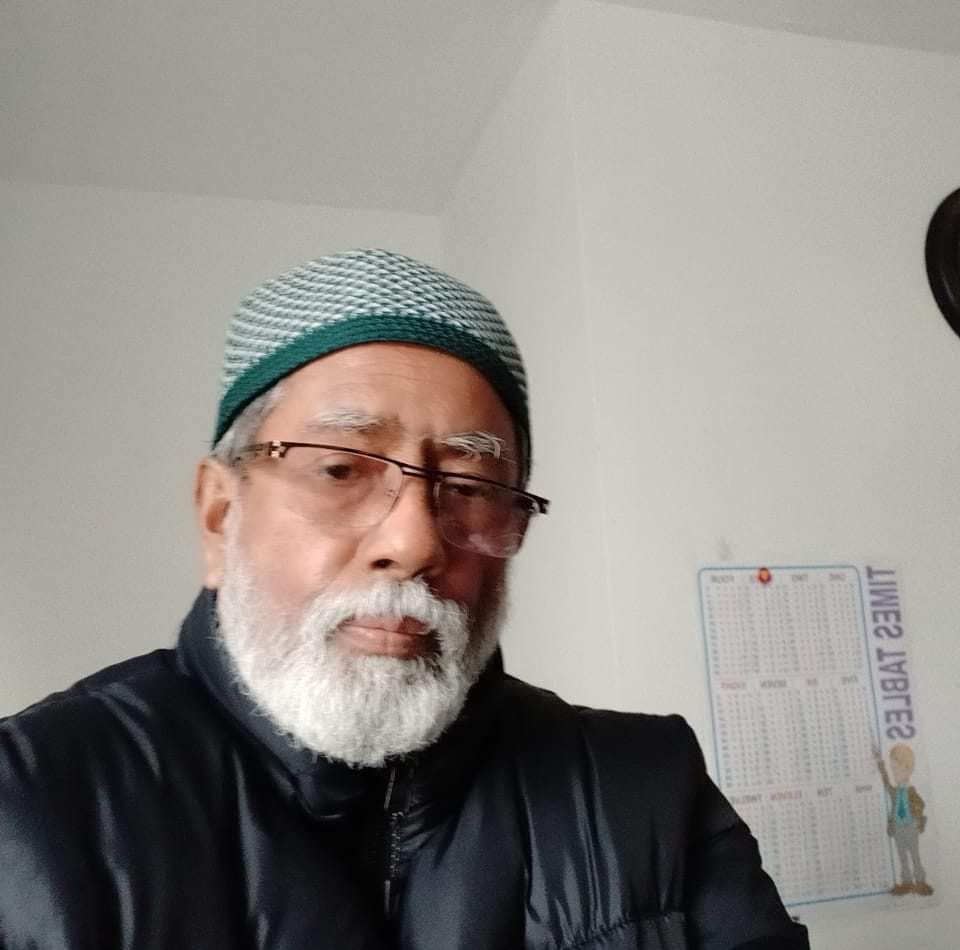



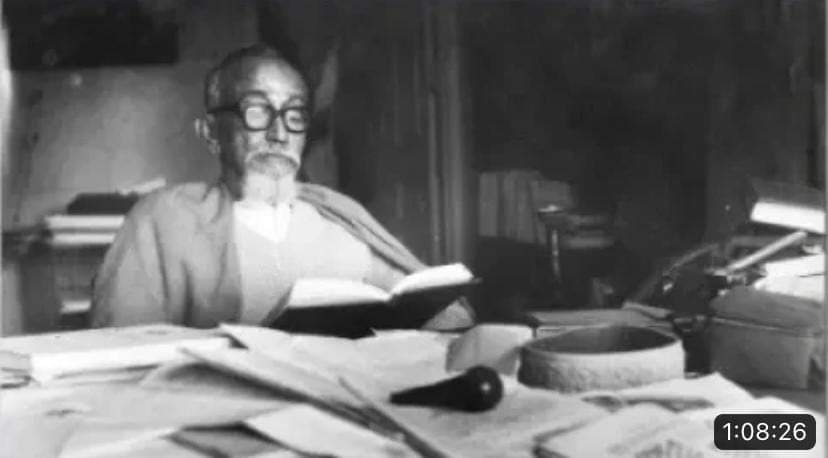
















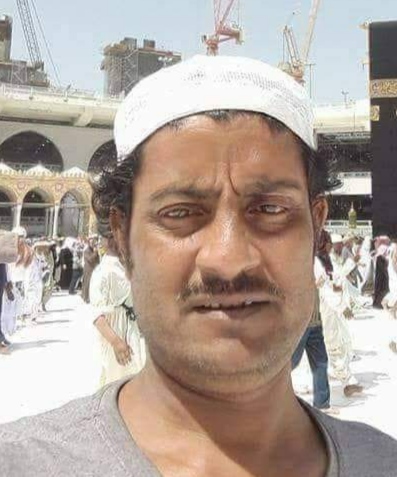


























































































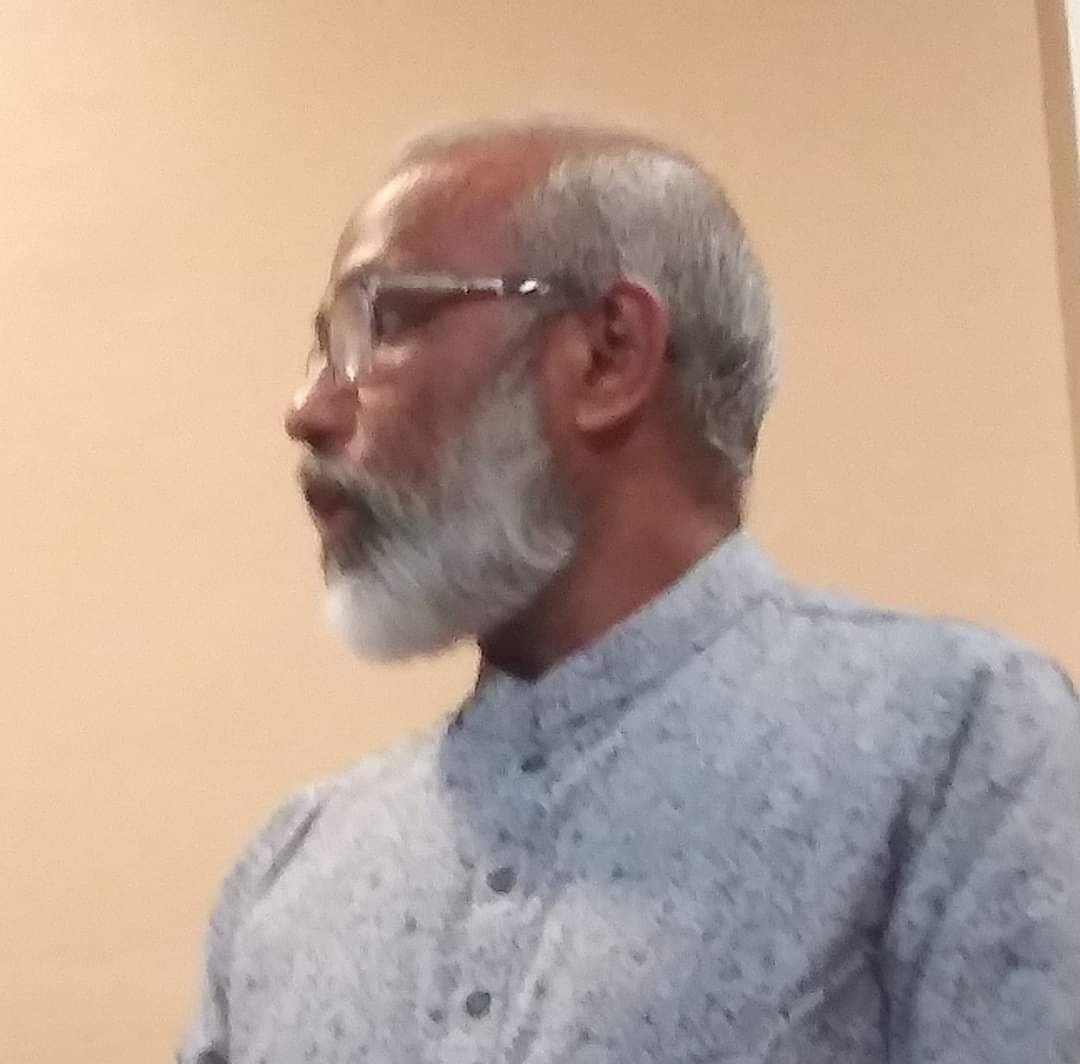








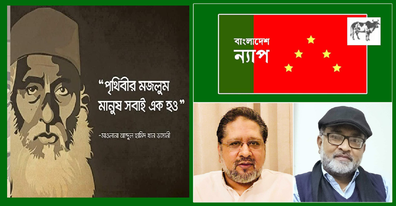

























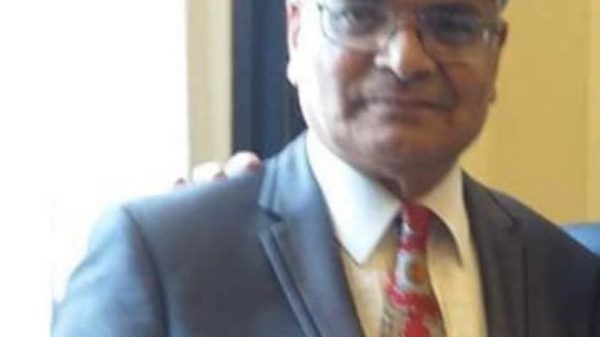
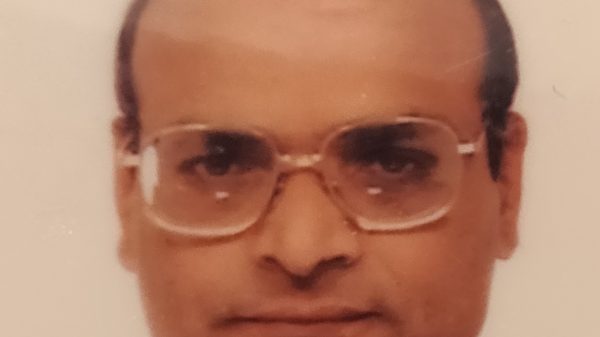












Leave a Reply